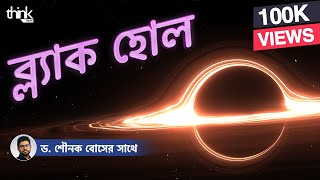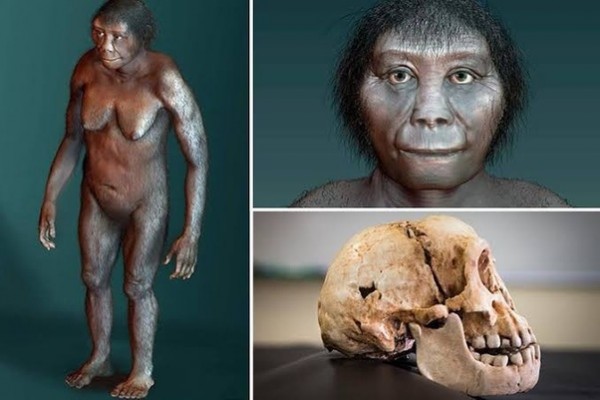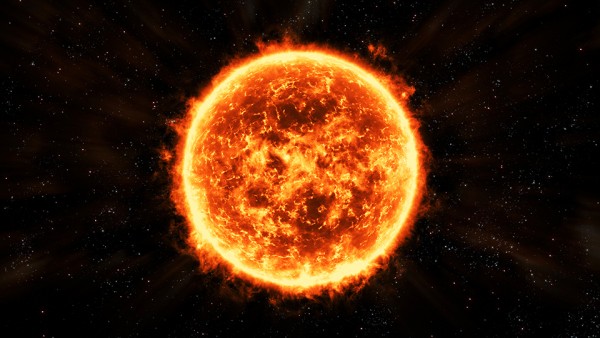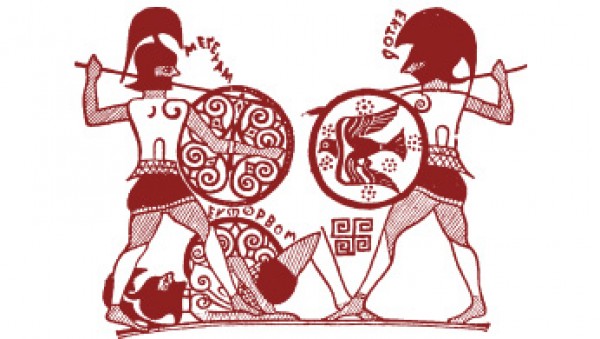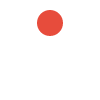ব্ল্যাক হোল বলতেই আমাদের মাথায় আসে এক বিশাল খাদক, হাঁ করে আশেপাশের সব কিছু গিলে ফেলছে। আমরা থিংকের ব্ল্যাক হোল ভিডিওতে দেখেছিলাম, জ্বালানী ফুরিয়ে যাওয়া তারা থেকে তৈরি এই মহাজাগতিক বা খগোল বস্তুগুলি মহাবিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণ আধার, ব্ল্যাক হোলকে ব্ল্যাক বা কৃষ্ণ বলা হয়, কারণ তাদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এত তীব্র যে এমনকি আলোও তাদের ভেতর থেকে বেরোতে পারে না।
এখন, একজন মানুষ যদি একটি ব্ল্যাক হোলের অমোঘ আকর্ষণে ধরা পড়ে? সে কি এমন এক অভিযাত্রায় বেঁচে থাকতে পারবে? চলুন, আজকের এই ভিডিওতে কল্পনার রথে চড়ে আমরা ঘুরে আসি একটা ব্ল্যাক হোলের কাছ থেকে, দেখি কী ঘটে।
ব্ল্যাক হোলের চারপাশে কী ঘটছে, তা বোঝার জন্য ব্ল্যাক হোলের সীমানা বা প্রান্ত বলতে কী বোঝায়, সেটা দেখা যাক।
এই সীমানার সংজ্ঞা বেশ সহজ। যে রেখা অতিক্রম করে গেলে ব্ল্যাক হোল থেকে আর ফেরত আসা যায় না, সেটাকেই ব্ল্যাক হোলের সীমানা বলে ধরা হয়। জাহাজ দিগন্ত পাড়ি দিলে যেমন সেটা আর দেখা যায় না, তেমনি কোনো বস্তু এই রেখা অতিক্রম করে গেলে সেই বস্তুর কী হয়, সেটা জানার কোনো উপায় থাকে না, তাই এই রেখাকে ব্ল্যাক হোলের ইভেন্ট হরাইজন বা ঘটনা-দিগন্ত বলা হয়। ২০১৯ সালে তোলা ব্ল্যাক হোলের যে ছবিটা আমরা অনেকেই দেখেছি, সেটা আসলে M87 গ্যালাক্সির কেন্দ্রের অতিভারী একটি ব্ল্যাকহোলের ঘটনা-দিগন্তের চারপাশের অতি উত্তপ্ত গ্যাস। বুঝতেই পারছেন, ঘটনা দিগন্তের ভেতরের কোনো ছবি তোলা সম্ভব না, কারণ ছবি তোলার মতো কোনো আলো সেই ব্ল্যাক হোল থেকে বের হতে পারবে না। আর এই গ্যাস যখন ব্ল্যাক হোলের আকর্ষণে তার ভেতরে পড়ে যাবে, তখন সেটাকেও আর দেখা যাবে না।
ঘটনা দিগন্তের কাছে আসার সাথে সাথে একজন মানুষের কী হবে? মজার ব্যাপার হচ্ছে, উত্তরটি কিন্তু সোজাসাপ্টা নয়। বিষয়টি নির্ভর করে ব্ল্যাক হোলটা কতটা বড়, তার ওপর। ভরের দিক দিয়ে ব্ল্যাক হোল কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ছোট ব্ল্যাক হোল, যদিও সেটা আসলে ছোট না, আমাদের সূর্যের ৫ থেকে ১০০ গুণ ভারী, যাকে আমরা stellar mass বা নাক্ষত্রিক ভরের ব্ল্যাক হোল বলতে পারি। আর অন্যটা হলো supermassive বা "অতিভারী" ব্ল্যাক হোল, যা ১০ লক্ষ থেকে ১০০ কোটি সৌরীয় ভরের হতে পারে।
মনে হতে পারে, যত বড় ব্ল্যাক হোল, তত বেশি তার ধংসাত্বক ক্ষমতা। অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, মহাকর্ষ সমীকরণ ব্যবহার করে দেখানো যায় যে আসলে নাক্ষত্রিক ভরের ব্ল্যাক হোল অনেক বেশি বিপদজনক। একটি ব্ল্যাক হোল কতটা বিপজ্জনক তা কেবল তার মোট মাধ্যাকর্ষণ কত সেটা নির্ধারণ করে না, বরং তার টাইডাল ফিল্ড বা জোয়ার-ক্ষেত্রের শক্তির পরিমাণ সেটা নির্ধারণ করে। এই টাইডাল বা জোয়ারের ফিল্ড হচ্ছে একটি বস্তুর দুই প্রান্তের মাধ্যাকর্ষন শক্তির পার্থক্যের পরিমাণ।
থিংকের জোয়ার ভাটা ভিডিওতে নিশ্চয় দেখেছেন, চাঁদ যে শুধু সমুদ্রের পানিকে টানে, তাই না; পৃথিবীর আকারকেও কিছুটা বিকৃত করতে পারে।
একটি ব্ল্যাকহোলও একই ভাবে তার আশেপাশের বস্তুতে জোয়ার এনে তার আকার বিকৃত করতে পারে।
নাক্ষত্রিক ভরের ব্ল্যাক হোলের জন্য ঘটনা দিগন্তের ব্যাসার্ধ, যা শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ নামেও পরিচিত, আমাদের দৈনন্দিন দূরত্বের সাথে তুলনীয়। যেমন, একটি ১০০ সৌরিয় ভরের ব্ল্যাক হোলের জন্য শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ প্রায় দুশো ছিয়ানব্বই কিলোমিটার। আবার সূর্যের সমান ভরের ব্ল্যাক হোলের জন্য শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ মাত্র দুই দশমিক নয় কিলোমিটার।
কিন্তু এক বিলিয়ন বা ১০০ কোটি সৌরীয় ভরের ব্ল্যাক হোলের শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ ৩০০ কোটি কিলোমিটার।
মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রতিটা জিনিসেরই শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ আছে। গড় ভরের একজন মানুষের শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধ হচ্ছে দশমিকের পরে ২২ টা শূন্য, তার পরে ১, অর্থাৎ একটা হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের চাইতেও ছোট। কিন্তু যেহেতু সেই ভর বিস্তৃত, তাই আমরা ব্ল্যাক হোল না। আর যে বস্তুর ব্যাসার্ধ তার শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধের চাইতেও ছোটো, সেগুলোই ব্ল্যাক হোল। অর্থাৎ প্রতিটা ব্ল্যাক হোলের ব্যাসার্ধ তার শোয়ার্জশিল্ড ব্যাসার্ধের চাইতে কম।
তাই যদি একজন মানুষ একটা ৩ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের ঘটনা দিগন্তের ব্ল্যাক হোলের দিকে পা নিচের দিকে দিয়ে পড়তে থাকে, তবে ১০০ কিলোমিটার দূরে থাকা অবস্থায় তার পা আকর্ষিত হবে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষনের চাইতে প্রায় বায়ান্নো হাজার গুন বেশি শক্তিতে। মাত্র দুই মিটার দুরের মাথায় আকর্ষন হবে তার চাইতে অনেক কম, অর্থাৎমানুষটার যে প্রান্ত ব্ল্যাক হোলের কেন্দ্রের অপেক্ষাকৃত কাছে, সেটাকে ব্ল্যাক হোলটি যে শক্তিতে আকর্ষণ করবে, অন্য প্রান্তকে তার চাইতে অনেক কম শক্তিতে আকর্ষণ করবে।
কিন্তু সেই তুলনায় একটা ৩০০ কোটি কিলোমিটার ব্যাসার্ধের ঘটনা দিগন্তের ব্ল্যাক হোলের তুলনায় একজন মানুষ এতই ক্ষুদ্র যে মানুষটা যেখানেই থাকুক না কেন, ব্ল্যাক হোল টি তাকে যে শক্তিতে আকর্ষন করবে, সেটার পরিমাণ তার শরীরের প্রতিটা অংশে প্রায় সমান হবে।
তাহলে কী দাঁড়ালো? যদি পা নিচের দিকে দিয়ে একজন মানুষ ব্ল্যাক হোলে পড়তে থাকে, তাহলে অপেক্ষাকৃত ছোট ব্ল্যাক হোলগুলি তার শরীরের কাছের প্রান্তে অর্থাৎ পায়ে, অন্য প্রান্তের বা মাথার তুলনায় অনেক বেশি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রয়োগ করবে।
কিন্তু মানুষের শরীরের চাইতে কোটি কোটি গুন বড় ঘটনা দিগন্তের ব্ল্যাক হোল তার শরীরের প্রতিটি বিন্দু থেকে আনুপাতিকভাবে মোটামুটি একই দূরত্বে আছে, ফলে মাথা এবং পায়ের ওপর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পার্থক্য হবে খুবই অল্প।
তাহলে সেরকম ছোট একটা ব্ল্যাক হোলে পড়ন্ত একজন মানুষের কী হবে? যেহেতু তার পায়ের ওপর আকর্ষণ অনেক বেশি হবে, ফলে তার শরীর টেনে ধরা ইলাস্টিকের মত লম্বা হয়ে যাবে এবং শরীর ছিঁড়ে না যাওয়া পর্যন্ত এই টান অব্যাহত থাকবে। ছিঁড়ে যাওয়া প্রতিটা টুকরাও আবার একই রকম অসম টান অনুভব করবে। এই টানে লম্বা হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটির নাম দেয়া হয়েছে স্প্যাগেটিফিকেশন। আক্ষরিক অর্থে এটা এমন একটা প্রক্রিয়া, যার ফলে মানব দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে স্প্যাগেটি বা নুডলসের মতো সরু ও লম্বা হতে থাকে।
আবার তার শরীরের প্রতিটা অংশ আড়াআড়িভাবে বিপরীত দিকে প্রচণ্ড টান খাবে, অর্থাৎ শরীরের ডান দিক বাম দিক দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে, বাম দিক ডান দিক দিবে বের হওয়ার চেষ্টা করবে।
ভয়াবহ এই শেষ পরিণতি! তবে এর ফলে ঘটনা দিগন্তে পৌঁছানোর আগেই শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, এভাবে ব্ল্যাকহোলের ভিতরে পড়ার অভিজ্ঞতার কোনো সুযোগ নেই মানুষের, এবং বর্তমানে কোনো ব্ল্যাক হোলের কাছে পৌঁছানোর প্রযুক্তিও নেই আমাদের। তবে আমরা ব্ল্যাক হোলের আকর্ষণে নক্ষত্রকে ছিন্নভিন্ন হতে দেখেছি। এই ঘটনাগুলিকে "জোয়ারে বিচুর্ণ করা" বা টাইডাল ডিজরাপশন ইভেন্ট বলা হয়। আর এই ছিন্ন বিচ্ছন্ন নক্ষত্রের অন্তর্গত উপাদানগুলির কিছু অংশ ব্ল্যাক হোলের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, আর কিছু অংশ চলে যায় ব্ল্যাক হোলের পেটের ভেতরে।
আর যদি কেউ একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলের দিকে পড়তে থাকে, তখন কী হবে? আগে যেমন বলেছি, এই ক্ষেত্রে জোয়ারের শক্তি সৌরীয় ভরের ব্ল্যাক হোলের মতো শক্তিশালী নয়, তাই এ ক্ষেত্রে স্প্যাগেটিফিকেশন ঘটবে না, যদিও শেষ ফলাফলটি এ ক্ষেত্রেও বিপর্যয়কর হবে। এখানেও চূড়ান্ত মাত্রার আকর্ষণ আছে, কিন্তু যেহেতু দেহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না, ফলে আমাদের পড়ন্ত মহাকাশচারীর জীবিত অবস্থায় ঘটনা দিগন্ত অতিক্রম করে ব্ল্যাক হোলের ভেতরে যাওয়ার এবং অবশেষে ব্ল্যাক হোলের কেন্দ্রের অদ্বৈত বিন্দু বা সিঙ্গুলারিটিতে পৌঁছানোর সম্ভাবনা আছে। তবে সেটা শুধু সম্ভব হতে পারে যদি ব্ল্যাক হোলটি আর কোন মহাজাগতিক গ্যাস বা নক্ষত্রকে হজম না করতে থাকে।
সেই মহাকাশচারী চারপাশে তাকালে দেখবে সবকিছু চূড়ান্ত রকম অদ্ভুত—সব কিছু আজবভাবে বেঁকে আছে, ব্ল্যাক হোলের ভেতরের চরম মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের কারণে অকল্পনীয়ভাবে প্রসারিত হয়ে আছে।
আরো মজার কথা হচ্ছে, অন্য কেউ যদি দূর থেকে সেই পড়ন্ত মহাকাশচারীকে দেখতে থাকতো, তাহলে সে দেখতো, মহাকাশচারী ঘটনা দিগন্তের কাছে পৌঁছাচ্ছে, কিন্তু ঘটনা দিগন্তে পড়ে যাওয়া বা পার হওয়ার দৃশ্য সে কখনোই দেখতে পেত না।
এর কারণটা আমরা শুরুতেই বলেছি—ব্ল্যাক হোল থেকে মহাকর্ষের কারণে আলোও বের হতে পারে না। আমরা চোখে দেখি বা টেলিস্কোপের লেন্স দেখে যখন আলো বা অন্যান্য তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণ রেটিনায় বা লেন্সে পড়ে। ব্ল্যাক হোল তো আলো বা অন্য কোনো তড়িৎ চুম্বকীয় বিকিরণকে বেরই হতে দেবে না, ফলে আমরা ঘটনা দিগন্ত পার হয়ে পড়ার দৃশ্য দূর থেকে কখনোই দেখতে পাবো না। দর্শকের কাছে মনে হয়, ঘটনা দিগন্তে চিরকালের জন্য মহাকাশচারী স্থির হয়ে আছে, যেন সেখানে সময়ও থেমে গিয়েছে, অথচ সে আসলে ব্ল্যাক হোলের ভেতরে।
ব্ল্যাকহোলের রহস্য অনেক। সায়েন্স ফিকশনে অন্য ইউনিভার্সে যাওয়ার দরজা হচ্ছে ব্ল্যাক হোল,অথবা টাইম ট্র্যাভেল করার জন্যও ব্ল্যাক হোলের ব্যবহার দেখেছি আমরা চলচিত্রে। হয়তো প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে আমরা সে সব রহস্যের সমাধানও পাবো।
আমাদের জনপ্রিয় ভিডিও দেখুন | Our Popular Videos
সবচেয়ে বেশি দেখা ভিডিও দেখুন | Most Watched Video
?>